মো. আসাদুজ্জামান
বর্তমান বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ তথ্যপ্রযুক্তি জগতে বিপ্লব এনেছে। চ্যাটবট, ছবি ও কনটেন্ট জেনারেশন টুল, কণ্ঠস্বর নকল প্রযুক্তি এবং স্বয়ংক্রিয় অনুবাদ ব্যবস্থা এখন আর বিলাসিতা নয়; বরং প্রতিদিনের জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই পরিবর্তন যেমন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, তেমনি সৃষ্টি করেছে নৈতিকতা, গোপনীয়তা এবং সর্বোপরি কপিরাইট আইনসংশ্লিষ্ট নানা জটিলতা। বাংলাদেশও এই নতুন প্রযুক্তির মুখোমুখি এবং এখনই সময় বিষয়গুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করে উপযুক্ত নীতিমালার পথ নির্ধারণ করা। এআই বর্তমানে অটোমেশন, কনটেন্ট নির্মাণ, অনুবাদ, ছবি ও সংগীত তৈরিসহ বহু কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। জনপ্রিয় এআই টুল, যেমন– চ্যাটজিপিটি, গুগল বার্ড, মিডজার্নি, ড্যাল-ই এবং অ্যাডোবি ফায়ারফ্লাই দিয়ে সহজেই লেখা, কোড, গান, চিত্র বা ভিডিও তৈরি করা সম্ভব।
বাংলাদেশে এই প্রযুক্তির প্রাথমিক ব্যবহার দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন খাতে। যেমন– শিক্ষা খাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা চ্যাটজিপিটি বা গুগল জেমিনি ব্যবহার করে রচনার ধারণা, গবেষণার সহায়তা এবং অনুবাদ কাজে নিয়োজিত হচ্ছেন। সংবাদপত্র ও ডিজিটাল মিডিয়ায় কনটেন্ট লেখায় এআইর সহায়তা নেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়াও সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, বিজ্ঞাপন ও গ্রাফিক ডিজাইনে এআই ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। তবে এসব ব্যবহার ঘিরে একটি মৌলিক প্রশ্ন সামনে এসেছে– এই কনটেন্টের কপিরাইট কার? এআই, নাকি মানুষের?
বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ হলো, প্রচলিত আইন প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না।
আমাদের কপিরাইট আইন অনুযায়ী শুধু ‘অথর’ বা ‘ক্রিয়েটর’ হিসেবে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এআই যেখানে স্বাধীনভাবে কনটেন্ট তৈরি করতে পারে, সেখানে আইনগত ভাষা অস্পষ্ট। এ ছাড়াও এআই কনটেন্ট যাচাইয়ের জন্য পরিকাঠামো নেই। কোন কনটেন্ট এআই তৈরি করেছে, তা শনাক্ত করতে বাংলাদেশে কোনো কেন্দ্রীয় টুল বা রেগুলেটরি সংস্থা নেই। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে এআই সম্পর্কিত কোনো পূর্ণাঙ্গ আইন বা নীতিমালা নেই। আইসিটি বিভাগ ২০২০ সালে একটি এআই রোডম্যাপ তৈরি করলেও কপিরাইটবিষয়ক নির্দেশনা অনুপস্থিত। এআই সম্পর্কিত জটিলতা সমাধানে আইনজীবী, পুলিশ ও বিচার বিভাগের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। এখনও সে প্রচেষ্টা সীমিত।
অপার সম্ভাবনার বাংলাদেশে এআই ব্যবহারের জন্য একটি সমন্বিত জাতীয় নীতি তৈরি করা জরুরি– যা প্রযুক্তির গবেষণা, উন্নয়ন, ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা, নৈতিকতা এবং মানবিক অধিকার রক্ষার দিক অন্তর্ভুক্ত করবে। ভারতের মতো অনেক দেশ ইতোমধ্যে এআই নীতিমালা তৈরি করেছে। বাংলাদেশেও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এ ধরনের নীতিমালা প্রয়োজন। এআই বিষয়ে আইন সংস্কার ও হালনাগাদ করতে হবে। কপিরাইট আইন ২০০০-এর পুনর্মূল্যায়ন করে এআইসংশ্লিষ্ট ধারাগুলো সংযোজন করতে হবে। এআই দ্বারা সৃষ্ট কনটেন্টের ক্ষেত্রে শেয়ারড ওনারশিপ বা ইউজার অ্যাট্রিবিউশন বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে। সংবাদপত্র, মিডিয়া, পত্রিকা, ইউটিউব চ্যানেল বা ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাতারা এআই ব্যবহার করলে তা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। এতে স্বচ্ছতা আসবে।
যেহেতু এআই প্রযুক্তি বিশাল পরিমাণ ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে, এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় একটি ডেটা প্রটেকশন আইন প্রয়োজন। যেখানে ডেটা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও শেয়ার করার নিয়মাবলি স্পষ্ট থাকবে। সরকার চাইলে স্বতন্ত্র এআই জেনারেটেড রেজিস্ট্রেশন প্ল্যাটফর্ম চালু করতে পারে। এই ডিজিটাল ডেটাবেজ চালু করে সেখানে এআইকৃত কনটেন্ট জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে কপিরাইট বিতর্ক এড়ানো যাবে। জাতীয় পর্যায়ে এআই নীতিমালা তৈরি করে সেখানে নৈতিকতা, কপিরাইট, ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বাংলাদেশ কপিরাইট অফিসকে ডিজিটাল যুগোপযোগী করা প্রয়োজন। মান্ধাতার আমলের সিস্টেম থেকে বের হয়ে এসে আধুনিক সিস্টেম চালু করতে হবে। কপিরাইট নিবন্ধন, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং পর্যালোচনা প্রক্রিয়া আরও আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় করা জরুরি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিঃসন্দেহে অগ্রগতির প্রতীক। তবে এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে না পারলে এটি সৃষ্টিশীলতা ও আইনগত কাঠামো বিঘ্নিত করতে পারে। বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান প্রযুক্তিনির্ভর দেশের জন্য এখনই সময় কপিরাইট আইনকে আধুনিকীকরণ এবং এআই ব্যবহারকে নিয়মের আওতায় আনার। সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাংলাদেশ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যুগে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দেওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারবে।
মো. আসাদুজ্জামান: সহকারী অধ্যাপক, আইন ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা











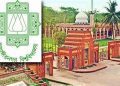






Discussion about this post