যদি প্রশ্ন করা হয় গবেষক বলতে আমরা কী বুঝি? বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কেন একজন ভালো গবেষক হওয়া প্রয়োজন? উত্তর, গবেষকরা হলো সেই মানুষ, যাদের মনে সদা নিত্যনতুন আবিষ্কারের নেশা কাজ করে, যাদের চিন্তাজুড়ে নতুন নতুন আইডিয়া কিলবিল করে। তারাই গবেষক। তারাই মূলত বিজ্ঞানী। এই গবেষকদের আমরা সাধারণত দুই ধরনের পেশায় দেখতে পাই। একদল গবেষক অ্যাকাডেমিয়ায় যুক্ত থাকেন। তারা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তারা প্রতি বছর নতুন নতুন গবেষকের জন্ম দেন। এদের একটি অংশ পরবর্তীতে ইন্ডাস্ট্রিতে চলে যায়। সেখানে তারা গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য করার জন্য কাজ করেন। কেউ কেউ নিজেদের স্টার্টআপ গড়ে তোলে এবং অনেকেই আর্থিকভাবেও সফল হন।
উদাহরণ হিসেবে বলা যায় BioNTech-এর প্রতিষ্ঠাতা দম্পতির কথা—তুর্কি বংশোদ্ভূত এই বিজ্ঞানীরা একসময় ছিলেন অ্যাকাডেমিয়ায় যুক্ত গবেষক। পরবর্তীতে স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠা করে আজ বিলিয়ন ডলার ভ্যালুয়েশনের একটি কোম্পানি দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু বিষয়টি মনে রাখা জরুরি—এই ইন্ডাস্ট্রি নিজে নতুন গবেষকের জন্ম দেয় না; বরং তারা ‘রেডিমেড’ গবেষক খুঁজে এনে তাদের নিয়ে কাজ করে।
তাহলে এই গবেষকরা কোথা থেকে আসে? উত্তর একটাই—অ্যাকাডেমিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই গবেষকদের জন্ম দেন। কারণ, গবেষণার বীজ বপন হয় বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে। শিক্ষার্থীরা যখন তাদের নিয়মিত কোর্স কারিক্যুলামের পাশাপাশি শিক্ষকের ল্যাবে গবেষণায় যুক্ত হয়, তখনই তাদের হাতে-কলমে গবেষণার হাতেখড়ি হয়। এরপর কেউ কেউ গবেষণায় উচ্চতর ডিগ্রি—পিএইচডি, পোস্টডক—অর্জন করে। কেউ ইন্ডাস্ট্রিতে যায়, কেউ অ্যাকাডেমিয়া বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ফিরে আসে এবং নতুন গবেষক তৈরির কাজ শুরু করে। এইভাবেই গবেষণার চক্র অব্যাহত থাকে—দশকের পর দশক। একজন ভালো গবেষকের অধীনে কাজ করতে পারলে এমনকি গড়পড়তা ছাত্রও অসাধারণ কিছু করে দেখাতে পারে।
উদাহরণ হিসেবে লুই পাস্তুরের কথাই ধরা যাক—অণুজীব বিজ্ঞানের জনক হিসেবে আমরা যাকে চিনি। অথচ ব্যাচেলর পর্যায়ে তিনি ছিলেন গড়পড়তা মানের ছাত্র। রসায়নে তার ফল ভালো ছিল না, বরং গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে তুলনামূলক ভালো ছিলেন। পরবর্তীতে এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী, ব্রোমিন আবিষ্কারক ব্যালার্ড তাকে নিজের ল্যাবে গবেষণা সহযোগী হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। আর সেখানেই পাস্তুর আমূল বদলে যান—একটির পর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে ওঠেন।
এখন প্রশ্ন হলো—যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিজেই গবেষক না হন, তাহলে কী হবে? সোজা কথা—সিস্টেম ভেঙে পড়বে। একজন শিক্ষক যখন গবেষণায় দক্ষ নন, তখন তার ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রও ভালো গবেষক হতে পারবে না। ফলস্বরূপ, ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুর্বল মানের গ্র্যাজুয়েট বের হবে, যারা না হতে পারে ভালো শিক্ষক, না ইন্ডাস্ট্রির চাহিদা পূরণ করতে পারবে। একসময় পুরো দেশ ‘Good for nothing’ গ্র্যাজুয়েট দিয়ে ভরে যাবে। এই চক্র একবার শুরু হলে, দেশ আর সহজে বের হতে পারবে না। এটি চোরাবালির মতো— হাতড়াতে হাতড়াতে তলিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। আমাদের দেশও এখন এমন চক্রে আটকে গেছে।
আমাদের দেশে গবেষণা না করেও মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে যাচ্ছেন, এমনকি পিএইচডি ছাড়াই কেউ কেউ অধ্যাপক পদে উন্নীত হচ্ছেন! সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্রে এসেছে, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি ছাড়াই ৪৩২ জন শিক্ষক অধ্যাপক পদে উন্নীত হয়েছেন। ভাবা যায়! অথচ বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগে পিএইচডি একটি মৌলিক শর্ত। পরে দেখা হয় পোস্টডক অভিজ্ঞতা, গবেষণা প্রকাশনা ও অ্যাকাডেমিক অর্জন। অথচ বাংলাদেশে অনার্স-মাস্টার্স পাস করেই অনেক তরুণ প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন—গবেষণা ছাড়াই। পরবর্তীতে যাদের বেশিরভাগ অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ বা গবেষণার পরিবর্তে শুধু প্রশাসনিক এবং শিক্ষকতা জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রশ্ন হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মানেই কি শুধু লেকচার দেওয়া, সিলেবাস শেষ করা আর পরীক্ষার খাতা দেখা? উত্তরটা যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?
বাস্তবে, একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে শুধু পাঠদান নয়, নতুন জ্ঞান সৃষ্টি এবং গবেষণার মাধ্যমে সমাজ ও জাতিকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার কাজও করতে হয়। আর এই গবেষণার কাজটি শুধুই ব্যক্তিগত কৃতিত্বের জন্য নয়— বরং এটি একটি দেশের সমগ্র উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা শুধু একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নয়। আমাদের পুরো উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় এই প্রবণতা বিদ্যমান। যার প্রকট প্রভাব পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয় র্যাংকিংয়ে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি র্যাংকিংয়ে ভারতের রয়েছে ৩০টির বেশি বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তানের ৮টি, শ্রীলঙ্কার ২টি, এমনকি নেপালেরও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম আছে। কিন্তু বাংলাদেশের একটিও নেই! ৩৫০ নম্বর পর্যন্ত খুঁজেও পাওয়া যায় না। অনেকেই এতে অবাক হন না। কারণ, বাংলাদেশে এখনও বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিয়োগ-বাণিজ্য এবং প্রশাসনিক সুবিধাপ্রাপ্তির জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
আরও পড়ুন-কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার এবং আমাদের চ্যালেঞ্জ
এখন প্রশ্ন হলো: এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের উপায় কী? প্রথমত, লেকচারার পদে নিয়োগ বন্ধ করে আন্তর্জাতিক রীতির মতো সরাসরি “সহকারী অধ্যাপক” পদে নিয়োগ চালু করতে হবে। নিয়োগের শর্ত হিসেবে পিএইচডি ও পোস্টডক গবেষণা অভিজ্ঞতা বাধ্যতামূলক করতে হবে। উন্নত দেশে থাকা গবেষকদের দেশে ফেরাতে রিভার্স ব্রেইন ড্রেইনের মতো উদ্যোগ নিতে হবে। আমি নিজে অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি, যারা বর্তমানে বিদেশে গবেষণায় যুক্ত। উন্নত, নিরাপদ পরিবেশ এবং আর্থিক সুযোগ-সুবিধার দিক থেকে বিদেশে তারা যেসব সুবিধা পাচ্ছে, তা আমাদের সরকারের পক্ষে দেওয়া কখনও সম্ভব নয়—এটা সবাই জানে। তা সত্ত্বেও, উচ্চশিক্ষিত এই তরুণ-তরুণীদের বড় একটি অংশ দেশে ফিরতে আগ্রহী। তাদের একটাই চাওয়া— নিজ দেশের মাটিতে একটি সম্মানজনক চাকরি। এই সুযোগ আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিতে পারতো। হতে পারতো ‘রিভার্স ব্রেইন ড্রেইন’-এর একটি কার্যকর ক্ষেত্র। এই কাজটি কার্যকর করা খুব বেশি কঠিন না। শুধু প্রয়োজন সদিচ্ছা। তবে একটি বড় বাধাও আছে। তা হলো— দুর্নীতি। অনৈতিক নিয়োগ, গবেষণাবিহীন পাঠদান আর রাজনৈতিক প্রভাবের চক্র থেকে বের না হলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নতির কোনও সম্ভাবনাই নেই।
এখন সময় এসেছে এই বিকারগ্রস্ত কাঠামো ভেঙে এক নতুন গবেষণাভিত্তিক অ্যাকাডেমিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার। গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেধাকেন্দ্রিক নিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক মানের অ্যাকাডেমিক সংস্কৃতি গড়ে তোলাই হতে পারে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা খাতের টার্নিং পয়েন্ট।
লেখক: পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চার, ভাইরাল ভ্যাক্সিন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, ন্যাশনাল হেলথ রিসার্চ ইনস্টিটিউট, তাইওয়ান।











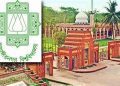





Discussion about this post