মুহাম্মাদ রাহাতুল ইসলাম
আধুনিক তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ‘সেলফ হেল্প’ এখন পপুলার কালচার। ইউটিউবের মোটিভেশনাল ভিডিও, ইনস্টাগ্রামের রিলস, অনলাইন কোর্স কিংবা নামি লেখকের সেলফ হেল্প বই—সবই যেন অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করছে, ‘তোমাকে আরও ভালো হতে হবে’। কিন্তু ক্রমাগত ‘নিজেকে উন্নত করার’ তাড়না অনেককে মানসিকভাবে ক্লান্ত ও স্থবির করে তুলছে। মনোবিজ্ঞানীরা এ ঘটনাকে বলেন সেলফ-হেল্প অ্যাডিকশন—অর্থাৎ আত্মোন্নয়নের নামে আত্মপ্রবঞ্চনা।
সেলফ হেল্প কনটেন্ট আসক্তির মূলে আছে ডোপামিন সার্কিট। ডোপামিন হলো মস্তিষ্কের একধরনের ‘রিওয়ার্ড কেমিক্যাল’, যা প্রত্যাশা ও উত্তেজনার সময় নিঃসৃত হয়। যখন কেউ একটি মোটিভেশনাল ভিডিও দেখেন বা অনুপ্রেরণামূলক উক্তি পড়েন, মস্তিষ্ক তাৎক্ষণিকভাবে ডোপামিন নিঃসরণ করে, যা তাকে অল্প সময়ের জন্য ভালো অনুভূতি দেয়।
কিন্তু সমস্যা হলো—এ উত্তেজনা দ্রুত হারিয়ে যায়। তখন আবার নতুন উৎস খোঁজা শুরু হয়: নতুন বই, নতুন স্পিকার, নতুন ভিডিও। ফলে ব্যক্তি এক অবিরাম ডোপামিন লুপে আটকে পড়েন—যেখানে শেখার আনন্দই হয়ে ওঠে আসক্তির কেন্দ্র কিন্তু বাস্তবে কোনো পরিবর্তন ঘটে না।
যুক্তরাষ্ট্রের নিউরোসায়েন্টিস্ট ড. অ্যান কিলি তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, ‘ডোপামিনের প্রত্যাশা-নির্ভর উদ্দীপনা মানুষকে এমন কাজের প্রতিও আকৃষ্ট করে, যা তাৎক্ষণিক সন্তুষ্টি দেয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে ফলহীন।’ এ কারণেই মোটিভেশনাল ভিডিও দেখা বা সেলফ হেল্প বই পড়া অনেকের কাছে কাজ করার চেয়ে সহজ ও সুখকর মনে হয়।
এক জরিপে (ম্যাককিনসে মাইন্ড রিপোর্ট ২০২৩) দেখা যায়, ৬৮% তরুণ প্রতিদিন অন্তত একবার মোটিভেশনাল কনটেন্ট দেখে, কিন্তু মাত্র ৯% সেই জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগ করে। এটি মনোবিজ্ঞানের এক পরিচিত ঘটনা—‘অ্যাকশন-নলেজ গ্যাপ’। অর্থাৎ আমরা জানি কী করতে হবে কিন্তু করি না।
এ ব্যবধানের পেছনে আছে সেলফ-হেল্প ইন্ডাস্ট্রির বাণিজ্যিক কৌশল। তারা প্রতিনিয়ত নতুন কোর্স, বই ও ওয়েবিনার ছুড়ে দেয় এই বার্তা দিয়ে যে, ‘তুমি এখনও যথেষ্ট নও, আরও কিছু দরকার।’ ফলে তরুণরা আত্মোন্নয়নের চক্রে আটকে যায়—যেখানে ‘শিখছি’ বলেই আত্মতুষ্টি আসে কিন্তু কোনো বাস্তব পরিবর্তন ঘটে না। মনোবিজ্ঞানীরা একে বলেন, ‘প্রোডাকটিভ প্রোক্রাসটিন্যাশন’—অর্থাৎ কাজের পরিবর্তে শেখার মধ্যেই আত্মতৃপ্তি খোঁজা।
অতিরিক্ত সেলফ হেল্প কনটেন্ট মস্তিষ্কে ইনফরমেশন ওভারলোড তৈরি করে। কগনিটিভ লোড থিওরি অনুযায়ী, মস্তিষ্কের তথ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষমতা সীমিত। প্রতিদিন অতিরিক্ত ‘কীভাবে উন্নত হওয়া যায়’ বার্তা পেলে মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ও মনোযোগ দুটোই দুর্বল হয়।
ব্রিটিশ জার্নাল সাইকোলোজিক্যাল সায়েন্সে প্রকাশিত এক গবেষণায় বলা হয়, তথ্যের অতিভার মানুষকে সিদ্ধান্তহীন ও অকার্যকর করে তোলে। তরুণরা তাই শেখে অনেক, ভাবে অনেক কিন্তু করে না কিছুই।
সেলফ হেল্প কালচার একটি নতুন মানসিক বিকৃতি তৈরি করছে—ক্রোনিক সেলফ-কমপ্যারিসন। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সবাই যেন উন্নত, উদ্যমী, সফল। ফলস্বরূপ, অনেক তরুণ নিজের বাস্তব জীবনকে তুচ্ছ মনে করতে শুরু করে। মনোবিজ্ঞানী ড. কারলিন গেইল বলেন, ‘অতিরিক্ত আত্মোন্নয়ন প্রচেষ্টা মানুষকে একসময় আত্মঅসন্তুষ্ট করে তোলে, কারণ সে সব সময় নিজের ঘাটতিই দেখতে পায়।’
এ মানসিকতা আত্মসম্মান নষ্ট করে এবং বিষণ্নতা বা ইমপোস্টার সিনড্রোম বাড়িয়ে দেয়—যেখানে ব্যক্তি মনে করেন, তিনি আসলে কিছুই অর্জন করতে পারেননি। তাই সবার প্রতি বাস্তবতার পথে ফেরার আহ্বান।
আত্মোন্নয়ন অবশ্যই জরুরি কিন্তু তা হতে হবে অ্যাকশন-ওরিয়েন্টেড। কেবল শেখা নয়, শেখাকে কাজে রূপান্তর করাই মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। মনোবিজ্ঞানীরা পরামর্শ দেন, প্রতিদিন একটি ছোট পরিবর্তনে মনোযোগ দিন—যেমন একটি ভালো অভ্যাস গঠন বা শেখা কোনো নীতি বাস্তবে প্রয়োগ। এটি ডোপামিন সিস্টেমকে ‘রিওয়ার্ড থ্রো অ্যাকশনে’ পুনঃসংবেদন করে, যা দীর্ঘমেয়াদি প্রেরণা জাগায়।










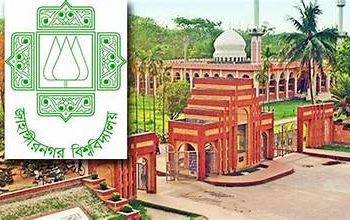






Discussion about this post